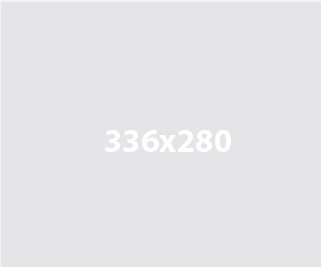By সজীব সরকার
বন্দীদশা থেকে মুক্ত হোক শৈশব, হোক আনন্দের
Media School July 31, 2024
আমাদের সমাজে শৈশব একরকমের ‘সশ্রম কারাবাস’ বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে না। কেন—তার ব্যাখ্যা দিচ্ছি।
মানুষের জীবনে খাওয়া-দাওয়া ও পড়াশোনা খুব জরুরি দুটি বিষয়। তাই, এ দুই বিষয়ে শৈশব থেকেই আগ্রহ ও আনন্দ—দুটিই থাকা জরুরি। কিন্তু, শিশুর জন্মের পর থেকেই এ দুটিকে শুধু অপছন্দের বিষয়ই নয়, রীতিমতো ‘শাস্তি’ বানিয়ে ফেলার প্রক্রিয়া শুরু হয়। সবাই না হলেও অনেক মা-বাবা বা অন্য অভিভাবক হয়তো বিষয়টি উপলব্ধিই করেন না; কিন্তু, নির্বিচারে এ কাজটি তারা করে যেতে থাকেন।
একটি শিশুর জন্মের পর থেকেই আত্মীয়-স্বজন থেকে শুরু করে এমনকি পাড়া-প্রতিবেশিরাও সদ্য মা হওয়া নারীটিকে অতিষ্ঠ করে তোলেন: ‘তোমার বাচ্চাকে ঠিকমতো খাওয়াও না? এতো শুকনা ক্যান? অমুকের বাচ্চাটাকে দেখেছো, কতো মোটাসোটা...।’ সদ্যভূমিষ্ঠ শিশুটি ফার্মের মুরগির মতো ফোলা-ফাঁপা না হলেই সবাই মা-কে রীতিমতো তিরস্কারে ভাসিয়ে দিতে থাকেন। এরপর শুরু হয় অমুক ফর্মুলা, তমুক ফর্মুলা খাইয়ে শিশুটির ‘মোটাতাজাকরণ’ পর্ব। এটি করতে গিয়ে শিশুদের স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি করা হয়, সেদিকে কারো নজর দেওয়ার সময় থাকে না।
ছয় মাস বয়স থেকে শিশুরা যখন একটু-আধটু করে সব ধরনের খাবার খেতে শুরু করে, ওই বয়সেই তাকে প্লেট ভরে ভরে খাওয়ানোর জন্য শুরু হয় নিপীড়ন। বড়রা ভুলে যান, তাদের নিজেদের পাকস্থলির আকার আর ওইটুকু শিশুর পাকস্থলির আকার এক নয়। এ ছাড়া, সব সময় সব শিশুর খাবারের চাহিদা, প্রয়োজন বা রুচি একরকম হয় না। অসুস্থ হলেও শিশুরা খাওয়ার রুচি বা আগ্রহ হারায়। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে খাবারের চাহিদা, রুচি, অভ্যাস ও শারীরিক গড়ন বদলাতেও থাকে। এই সহজ বিষয়টি অভিভাবক বা প্রতিবেশি - কেউই বুঝতে চান না বা মেনে নিতে পারেন না। ফলে, শিশুটি স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠছে কি না, বা সে শারীরিক-মানসিকভাবে প্রফুল্ল আছে কি না - এই সহজ বিষয়টিকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে সে গোগ্রাসে খাবার গলাধঃকরণ করছে কি না। যদি না করে, তাহলে বকাঝকা এমনকি মারধোর করে হলেও তার মুখে খাবার ঠেসে দেওয়া হয়।
বেঁচে থাকার জন্য খাবার অপরিহার্য। তবে, স্থান-কাল-পাত্র বা পরিস্থিতিভেদে এর পরিমাণ ভিন্ন হতে পারে। জোর করে না গিলিয়ে বরং শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করা উচিত- খাওয়া-দাওয়া করা কেন দরকার। আর, খাবারের পরিমাণের দিকে বেশি আগ্রহী না হয়ে এর পুষ্টিগত মানের দিকেই মনোযোগী হওয়া উচিত। প্রতিদিন প্রতি বেলায় থালা ভরে না খেলেও পুষ্টিকর খাবার পরিমাণে কিছুটা কম খেলেই বা ক্ষতি কী?
আর, শিশুদের হাতে কিছুটা ক্ষমতা ছেড়ে দিলেও ক্ষতির তো কিছু নেই; খাবারের গুরুত্ব বুঝতে পারলে সে নিজেই একটু-আধটু করে হলেও খেতে থাকবে। ঘড়ি ধরে সবসময় ক্ষুধা না-ই লাগতে পারে। কোনো একদিন কোনো এক বেলায় কিছুই খেতে ইচ্ছে না-ই করতে পারে। বাধ্য হয়ে খাবার গেলা বা বিরক্ত হয়ে একেবারেই না খাওয়ার চেয়ে সেটিই ভালো নয় কি?
এরপর আসে পড়ালেখার প্রসঙ্গ। খুব কম বয়সেই শিশুদের স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়। আজকাল দু-তিন বছর বয়সেই ‘প্লে গ্রুপ’ বা নার্সারি দিয়ে শিশুদের শিক্ষাজীবন শুরু হয়। শ্রেণির নামই ‘প্লে গ্রুপ’; অর্থাৎ, এ সময় স্কুলে যাওয়ার উদ্দেশ্য হবে কেবল অন্য শিশুদের সঙ্গে খেলাধুলা করা। এ সামাজিকীকরণের মধ্য দিয়েই তারা নানা কিছু শিখবে। নার্সারিতে শিশুরা মজার মজার ছড়া পড়বে কেবলই আনন্দের জন্য। কিন্তু, তা না করে, অভিভাবকদের অস্থির হয়ে উঠতে দেখা যায় এমন দুর্ভাবনায়—‘স্কুলে যাচ্ছে, কিন্তু অ্যালফাবেট, নাম্বারস বা রাইমস শিখছে না কেন?’
প্লে বা নার্সারি পার করতে করতে শিশুরা ‘বিদ্যাসাগর’ কেন হয়ে উঠছে না- এ জন্য শুরু হয় স্কুল বদলের পালা। নামকরা স্কুল, কড়া শাসনের স্কুল, বেশি বেশি বই পড়ানো স্কুল, ভালো রেজাল্ট করা স্কুল, ভালো কোচিং করানো টিচারদের স্কুল, শতভাগ জিপিএ-৫ পাওয়া স্কুল...। শিশুরা যেন ওইসব স্কুলের ভর্তি পরীক্ষায় পাস করতে পারে, এ জন্য ওইটুকু বয়সেই তাদের অংক-ইংরেজি গেলানোর ধুম পড়ে যায়। নার্সারিতে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতির কোচিংয়ের বিজ্ঞাপনও রাজধানীর দেয়ালে একেবারে বিরল নয়। বেচারাদের অবস্থা রবীন্দ্রনাথের ‘তোতাকাহিনীর’ সেই তোতা পাখিটির চেয়ে কিছু কম নয়—যেখানে ‘বিদ্বান’ বানাতে শেষ পর্যন্ত তোতাটিকে আক্ষরিক অর্থেই বই ছিঁড়ে গেলানো হয়েছিল!
সেই সাতসকালে স্কুলের শুরু, এরপর দিনভর কোচিংয়ের ব্যাচ আর ঘরে প্রাইভেট টিউটর। অনেকের তো আবার সকালে স্কুল শুরুর আগেও একবার ব্যাচে পড়ে তবে দিনের শুরুটা হয়! দিন-রাত পড়াশোনা আর হোমওয়ার্ক; এগুলো সব ঠিকমতো করার শর্তে বিকেলে বা সন্ধ্যায় একটু খেলার অবসর মেলে। কিন্তু, শৈশব কি বরং এর উল্টোটা হওয়ার কথা ছিল না?
শৈশবে শিশুদের প্রথম ও সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হতে হবে খেলাধুলা। তারা খেলবে। মনের আনন্দে খেলবে। ছুটোছুটি করবে। ছবি আঁকবে। নাচ-গান-আবৃত্তি - যার যা ভালো লাগে, তা-ই করবে। শিশুরা নিজেদের মধ্যে মান-অভিমান করবে, ঝগড়া করবে; আবার দ্বন্দ্ব মিটিয়ে মিলে যেতেও শিখবে। এর মাঝে মাঝে বয়সের সঙ্গে সঙ্গে একটু একটু করে পড়ালেখার পরিমাণ বাড়বে। আর, সেটিও হতে হবে তার সম্মতিতেই। তাকে শুরু থেকেই বোঝাতে হবে, জীবনের জন্য পড়াশোনা করা কেন ও কতোটা জরুরি। তাকে এটি বুঝিয়েই খানিকটা করে পড়াশোনা করাতে হবে; জোরজবরদস্তি করে নয়। মাঝে-মধ্যে দু-একদিন স্কুল কামাই দিলেই বা ক্ষতি কী? একদিনেই কি সে সবকিছু শিখে ফেলবে বা জীবনের সবকিছু মিস করে ফেলবে?
শৈশব হবে মূলত খেলাধুলার সময়; এর মধ্যে একটু-আধটু করে পড়াশোনা। কিন্তু, আমরা এর উল্টোটা ঠিক করে দিয়েছি; শৈশব এখন মূলত পড়াশোনা, আর এর মাঝে অবসর পেলে তবেই খানিকটা খেলাধুলা। এমনটা হলে শৈশব থাকল কোথায়!
বড়দের নিজেদের শৈশবের কথা মনে করে দেখা উচিত—খাওয়া আর পড়ার ব্যাপারে তাদের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল। বড়রা তো কারণে, অকারণে খাওয়া-দাওয়ায় অনিয়ম করে; কিন্তু, শিশুরা একবেলা খেতে না চাইলেই শুরু হয় জোরজবরদস্তি। শিক্ষক বা চিকিৎসকসহ এমন অনেক পেশার ব্যক্তির সবসময় পড়াশোনার দরকার পড়ে; তাই বলে আমরা বড়রাই কি প্রতিদিন নিয়ম করে বই পড়ি? মাঝে-মধ্যেই কি অলসতা বা অন্য কোনো কারণে পড়ায় ‘ফাঁকি’ দিই না? প্রতিদিন কি নিয়ম বেঁধে অফিসে যেতে ইচ্ছে করে? কোনোদিন কি বিশ্রাম কিংবা বেড়ানো বা আড্ডার জন্য অফিস কামাই দিই না? তাহলে, শিশুরা একদিন স্কুল কামাই দিয়ে ঘুমোতে চাইলে বা বাসায় থাকতে চাইলে এত জবরদস্তি কেন?
আমার নিজের সন্তানেরই একটি উদাহরণ দিই। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ার সময় আমার সন্তান মাঝে-মধ্যেই স্কুলে যেতে চাইতো না। কোনোদিন তাকে জোর করে স্কুলে পাঠাইনি। আমার মতে, ইচ্ছের বিরুদ্ধে তাকে স্কুলে পাঠালে ওইদিন কোনো ক্লাসেই সে মনোযোগ দিতে পারবে না বা কিছু শিখতে পারবে না। তাই, যেদিনই সে যাবে না বলেছে, একবারেই রাজি হয়েছি। তবে, তাকে বলেছি, ‘তোমার কথা রাখলাম; এখন তুমি যদি আমার একটা কথা রাখো, তাহলে খুশি হবো। কথাটা হলো—বাসায় থেকে খেলাধুলা-দুষ্টুমি সবই করবে, তবে, মাঝে-মধ্যে একটুখানি গল্পের বই পড়বে, গান শুনবে, ছবি আঁকবে বা সিনেমা দেখবে। এসবের মধ্যে তোমার যা ভালো লাগে, করতে পারো। তবে, করতেই হবে—এমনও নয়। কোনো চাপ নেই। ইচ্ছে হলেই কোরো।’ সে কখনো কথা রেখেছে, কখনো রাখেনি। তবে, যেদিন কথা রাখেনি, সেদিন তা নিজেই সরল মনে স্বীকার করেছে। বলেছি, ‘ঠিক আছে। আজ ইচ্ছে করেনি যেহেতু, তাই সমস্যা নেই। ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছুই করতে হবে না। যেদিন ইচ্ছে করে, সেদিন কোরো।’ পরে দেখেছি, অন্যদিন ঠিকই এগুলো করেছে। আনন্দ নিয়েই করেছে। আর, এখন তাকে দেখি, রোদ-ঝড়-বৃষ্টি-বন্যা-অবরোধ যা-ই থাক, সে প্রতিদিন স্কুলে যেতে চায়। স্কুল ছুটি থাকলে সে বিরক্ত হয়, মন খারাপ করে থাকে।
আরেকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। আমাদের সন্তানের জন্মের পর থেকে তার স্বাস্থ্য খুব ঘনঘন বদল হয়েছে। কদিন পরপরই খুব শুকিয়ে যেত, কদিন পর আবার ঠিক হয়ে যেত। ওর স্বাস্থ্য নিয়ে অনেকেই অনেক কিছু বলেছে; আমি বা আমার জীবনসঙ্গী তাতে কর্ণপাত করিনি। আমরা কখনোই বেশি বেশি খাওয়ানোর বা জোর করে খাওয়ানোর চেষ্টা করিনি। বরং, পরিমাণে কম খেলেও অন্তত ফল-দুধ-ডিমের মতো দরকারি খাবারগুলো প্রতিদিনই একটু-আধটু করে খাওয়ানোর চেষ্টা করেছি। আমাদের সন্তান এখন নিজে থেকেই রুচি অনুযায়ী কম-বেশি খাওয়া-দাওয়া করে। মাঝে-মধ্যে খেতেই চায় না, আবার কখনো নিজেই চেয়ে খায়। খাবারের পরিমাণ নিয়ে আমরা কখনোই কিছু বলি না; দরকারি উপাদানগুলো তার খাবার-দাবারে থাকছে কি না, শুধু এটুকুই নজরে রাখি।
আমরা বড়রা খাওয়া-দাওয়া আর পড়াশোনা নিয়ে শিশুদের ওপর এমন অবৈজ্ঞানিক চাপ তৈরি করি, যা জীবনের জন্য জরুরি এই দুটি বিষয়ের প্রতিই তাদের অভক্তি তৈরি করে। এ দুই বিষয়ে বড়দের অযৌক্তিক আচরণের কারণে খাওয়া আর পড়ালেখা শিশুদের কাছে ভীতিকর শুধু নয়, রীতিমতো ‘শাস্তি’ হয়ে ওঠে। অনেক অভিভাবক সন্তানকে আক্ষরিক অর্থেই ‘শাস্তি’ হিসেবে জোর করে পড়ার টেবিলে বসিয়ে দেন। এর পরিণতি কী? পড়াশোনার ব্যাপারে শিশুদের মনে তখন কী ধারণা জন্ম নেয়? পড়াশোনা করাটাকে তারা তখন ‘শাস্তি’ হিসেবেই দেখে এবং ঘৃণা করতে শুরু করে।
প্লে থেকে শুরু করে অন্তত নবম শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষার ফলাফল তো কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি কিংবা চাকরির নিয়োগের সময় ঘেঁটে দেখা হয় না; তাহলে, ওই ক্লাসগুলোতে পরীক্ষায় প্রথম হওয়া বা প্রথমদিকে থাকার চাপ কেন দেওয়া হয় শিশুদের? আর, একটি ক্লাসে ৩০ জন শিক্ষার্থী যদি থাকে, তাহলে ৩০ জনেরই মা-বাবার প্রত্যাশা থাকে- তাদের সন্তানকেই ক্লাসে প্রথম হতে হবে। এটি কী ধরনের যুক্তি হলো? ৩০ জনই কী করে প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় হবে?
এমন অযৌক্তিক চাপ তৈরি না করে যদি প্রতি ক্লাসের সঙ্গে মিল রেখে জরুরি বিষয়গুলো জীবনের জন্য, আনন্দের জন্য জানার ব্যাপারে শিশুদের আগ্রহী করা হয়, তাহলে শিশুরা চাপ বোধ করবে না; বরং সত্যিকার অর্থেই তারা কিছু শিখবে, পরীক্ষাতেও ভালোই করবে। তবে, মনে রাখতে হবে, কেবল পরীক্ষার ফল দিয়ে শিক্ষার্থীদের মেধা বা জানা-শোনার পরিধি নির্ভরযোগ্যভাবে বিচার বা নির্ণয় করা সম্ভব নয়, উচিতও নয়। তাই, তারা প্রতিদিন নতুন কিছু শিখছে কি না—এ বিষয়েই বরং বেশি মনোযোগী হওয়া দরকার।
বড়দের বোঝা উচিত, সবাই সব বিষয়ে সমান পারদর্শী হবে না। দু-একবার পরীক্ষার ফল খারাপ হওয়াটাও অস্বাভাবিক বা অন্যায় কিছু নয়। তাই, এ নিয়ে বকাঝকা বা মারধোর না করে বরং বিষয়টি সহজভাবে নেওয়া দরকার। তাকে জিজ্ঞেস করতে হবে- কেন খারাপ হলো, তার কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না, বা কী করলে সামনে ভালো করতে পারবে। এমন সহজ ও আস্থাপূর্ণ যোগাযোগের বদলে ভীতিকর পরিবেশ তৈরি করে রাখার কারণেই শিক্ষার্থীরা পরীক্ষায় খারাপ করলে আত্মহত্যার মতো সিদ্ধান্ত নেয়।
শিশুদের শারীরিক-মানসিক সুস্থতার জন্য খেলাধুলা ও পুষ্টিকর খাবার জরুরি। সেই সঙ্গে পরিবারের মধ্যে সুস্থ ও আনন্দময় পরিবেশ থাকাও খুবই জরুরি একটি বিষয়। শিশুদের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সুবিধা-অসুবিধা বা আগ্রহের কথা জিজ্ঞেস করা, মনোযোগ দিয়ে তাদের কথা শোনা এবং তাদের কথাগুলো যতোটা সম্ভব রাখার চেষ্টা করা জরুরি। শিশুরা পরিবারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সদস্য—এটিও তাদের বুঝতে দেওয়া দরকার। শিশুর জন্য তার পরিবার সবচেয়ে নিরাপদ ও ভরসার আশ্রয়স্থল হতে হবে এবং এই আস্থা যেন তাদের মধ্যেও তৈরি হয়, সেটি নিশ্চিত করতে হবে। ছোট ছোট বিষয়ে শিশুদের সঙ্গে আলোচনা করলে এবং যথাসম্ভব তাদের সিদ্ধান্তকে গুরুত্ব দিলে তারা আত্মবিশ্বাস নিয়ে বেড়ে ওঠার সুযোগ পায়। আর, মা-বাবার সঙ্গে সহজ ও সততার সম্পর্কও তৈরি হয়।
আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বোঝাতে হবে যে, তার নিজের জীবন-জীবিকার মান বাড়াতেই ভালোমতো পড়াশোনা করা জরুরি। তবে, এজন্য কোনোভাবেই তাদের শ্রেণিকক্ষ, কোচিং ও পাঠ্যবইয়ের ওপর নির্ভরশীল করে রাখলে হবে না; জীবনের জন্য জরুরি বিষয়গুলো জানা সম্ভব আসলে শ্রেণিকক্ষের বাইরে, পাঠ্যবই থেকে মুখ তুলে চারপাশে তাকালে। এই বোধটুকু শিশুদের মনে জাগ্রত করতে হবে। তাই, ধরে-বেঁধে প্রতিদিন স্কুলে পাঠাতে হবে এবং বইপত্র প্রয়োজনে ‘গিলিয়ে’ হলেও সব মুখস্থ করাতে হবে—এমন ভ্রান্ত ধারণা থেকে অভিভাবকদের বেরিয়ে আসা দরকার।
খেলাধুলা, বিনোদন, সাহিত্য পাঠ, ভালো গান শোনা, ভালো সিনেমা দেখা, নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক আড্ডা ও দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা থেকে শিশুরা যা শিখতে পারবে, তা কোনো স্কুল বা কোনো শিক্ষক তাদের শেখাতে পারবে না। দিন-রাত পড়াশোনা, পরীক্ষার প্রস্তুতি আর রেজাল্টের আতঙ্ক শিশুদের জীবন থেকে তাদের সবচেয়ে আনন্দের ও সবচেয়ে মূল্যবান সময় সেই শৈশবকেই কেড়ে নিয়েছে। জেলবন্দী কয়েদির সঙ্গে শিশুদের জীবনের তাহলে পার্থক্য আসলে কতটা?
শিশুদের এমন নিরানন্দ জীবনের অবসান হোক। শৈশব হোক নির্মল আনন্দের; শুধুই আনন্দের, উৎসবের। শিশুদের এই আনন্দের সুযোগ তৈরি করে দিলে, তাদের মতামতের গুরুত্ব দিলে ও তাদের নিজেদের মতো করে ব্যক্তিত্ব গড়ে ওঠার সুযোগ করে দিলে তারা স্বাভাবিকভাবেই নিজেদের প্রতি যত্নশীল হতে শিখবে। খাওয়া ও পড়ার গুরুত্ব বুঝতে শিখবে। জীবনের জন্য জরুরি বিষয়গুলো আগ্রহ ও আনন্দ নিয়ে শিখতে চেষ্টা করবে। বড়দের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে। প্রকৃত অর্থেই সুশিক্ষিত ও ভালো মানুষ হবে।
‘বন্দীদশা’ থেকে মুক্ত হোক আমাদের সন্তানেরা; আনন্দে উচ্ছল থাকুক শৈশব!
*লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় ইনডিপেনডেন্ট ডিজিটাল-এ, ৩১ জুলাই ২০২৪। সম্পাদকীয় বিভাগের মৌখিক অনুমতিক্রমে পুনঃপ্রকাশিত।